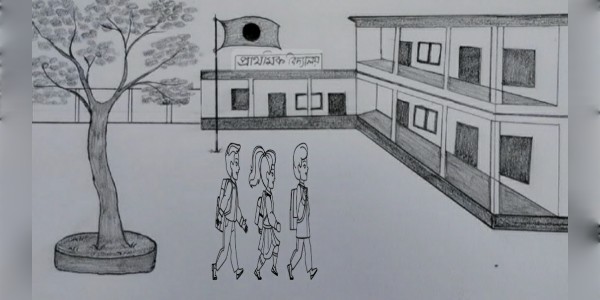তিনি কি সত্যিই স্ট্রিট লাইটের নীচে পড়তেন? ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় স্ট্রিট লাইট ছিল কি?
তিনি কি সত্যিই “নাস্তিক” ছিলেন? তাহলে জীবনের শেষ বেলায়ও সন্ধ্যা-আহ্নিক কেন করতেন? কেন আমৃত্যু পৈতে ছিল তাঁর….!!
এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন ড. প্রশান্ত চক্রবর্তী।
বিদ্যাসাগর-বিষয়ক কিছু মিথ, কিছু সত্য : ফিরে দেখা।
প্রশান্ত চক্রবর্ত
বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর সুবল মিত্রের বিদ্যাসাগর-জীবনী ছাড়া বাদবাকি অনেকগুলো নতুন-পুরনো প্রখ্যাত বিদ্যাসাগর-চরিত এই মুহূর্তে ঘাঁটাচ্ছি। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, সন্তোষচন্দ্র অধিকারী, সৌমেন্দ্রনাথ সরকার থেকে শুরু করে বিনয় ঘোষ, শংকরীপ্রসাদ বসু, ইন্দ্র মিত্র…। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কত গল্প কত কাহিনি প্রচলিত~সেসবের উৎস খুঁজতে গিয়ে কিছু সংশয় কিছু প্রশ্ন উঠে এল। সংক্ষেপে দু-একটি তুলে ধরছি।
১.
.”কলকাতায় বিদ্যাসাগর রাস্তার আলোয় পড়তেন”~এইরকম একটা কথা বঙ্গভুবনের বাজারে চালুু আছে। কিন্তু অতগুলো বিদ্যাসাগরজীবনী ঘাঁটানোর পরও এই “রাস্তার আলো”য় পড়ার বিস্তারিত বিবরণ পেলাম না। শম্ভুচরণের বইয়ে আছে কিনা জানি না। স্বয়ং বিদ্যাসাগর যে-খণ্ডিত আত্মজীবনচরিতটি লিখে গেছেন, সেখানেও নেই। রাস্তায় সরকারি আলোয় দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করাটা কিন্তু বিরল অভিজ্ঞতা। সারাজীবন ভোলার মতো নয়। বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মকথনে একটা বাক্যও এই নিয়ে খরচ করেননি। শুধু সন্তোষকুমার অধিকারীর বইয়ে আছে~”রাত্রে রান্না হয়ে গেলে তাঁর পড়াশোনা করার সময়। সরষের তেলের প্রদীপে তিনি পড়তেন; তেল ফুরিয়ে গেলে রাস্তার আলোতে।” (‘বিদ্যাসাগর’,সন্তোষকুমার অধিকারী, রূপা, প্রথম সং, ১৯৭০,পৃ. ৪)। কিন্তু তথ্যটির কোনো উৎস নেই।
১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি আট বছর বয়সের বালক বিদ্যাসাগরকে কলকাতায় আনা হয়। কলকাতা বলতে তো তখন গ্রাম-গ্রাম চেহারার একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। বড়বাজার অঞ্চলের দয়েহাটা। বাঙালি শেঠদের কিছু দালানবাড়ি, পুকুর, বাগান, বাঁশবন, বাঁশঝাড়, পায়ে হাঁটা মেঠোপথ। তারই মধ্যে বাণিজ্য। ব্যবসায়কেন্দ্র। গদি। দয়েহাটার কোনো একটি গলিতে ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতে আশ্রয়। তখন এই কলকাতায় রাস্তায় আলো জ্বলত বলে কোনো তথ্যই কিন্তু নেই।
এই চিত্রের বিপরীতে কলকাতার পথের আলোর বিষয়ে একটি তথ্য দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের একটি আত্মজীবনী “ছেলেবেলা”। ওতে তিনি লিখেছেন~
“তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি;কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে আলো জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।”(“ছেলেবেলা”, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭১২)
এই বর্ণনা মোটামুটি ১৮৭০-এর। তাহলে ১৮২৮-এ যখন বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন, তখন কলকাতার রাস্তায় কীসের আলো জ্বলত~সেটা ভাববার বিষয় নয় কি?
তাহলে এটাও কি দামোদর নদী সাঁতরে পার হওয়ার মতনই কিংবদন্তিকাহিনি?!
২.
বিদ্যাসাগরকে “নাস্তিক” তথা “অধার্মিক” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বহু চেষ্টা বঙ্গভুবনে করা হয়েছে। এ নিয়ে অজস্র আলোচনা আছে। পক্ষে-বিপক্ষে জোর গলায় তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। কেউ-কেউ তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বা ‘অ্যাগ্নস্টিক’ও বলতেন। এ-বিষয়ে প্রথম হাওয়া গরম করেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত কাছের লোক ছিলেন। নিজেই দাবি করতেন, তিনি যতটা বিদ্যাসাগরকে জানেন~আর কেউ জানে না। কৃষ্ণকমল প্রথম প্রচার করেন~বিদ্যাসাগর পাড় “নাস্তিক”।
এই বিষয়টি পরে মার্কসবাদীরা লুফে নেয়। হইচই করে। অন্তত তাঁদের মতাদর্শে একজন বড় বাঙালিকে নমুনা হিসাবে দেখানো যাবে। ধর্মকে “আফিম” রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁদের গুরুমশাই মার্ক্স। বিদ্যাসাগরও অধার্মিক ছিলেন। একে একে দুই। কিন্তু এদেরই একটি উগ্র ডাল নকশালরা বিদ্যাসাগরকে ‘ব্রিটিশের গোলাম’ চিহ্নিত করে তাঁর মূর্তি ভাঙা শুরু করেছিল।
বিদ্যাসাগর যে “নাস্তিক” ও ধর্মীয় দর্শন বিরোধী ছিলেন~তার জোরালো প্রমাণ স্বরূপ প্রথমত ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর তৎকালীন শিক্ষা পরিষদের সচিব এফ. মোয়াট সাহেবকে একটি লম্বা চিঠির উল্লেখ করা হয়। সেখানে বেদান্ত ও সাংখ্যকে ‘ভ্রান্ত দর্শন’ লিখেছিলেন তিনি। চিঠিটির বয়ান এরকম~
“That Vedanta and Sakhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute…”
তাঁর জীবনীকারেরাও প্রথমদিকে চিঠিটির কথা জানতেন না। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি উদ্ধার করে ছাপিয়ে দিতেই অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। পেয়েছি, পেয়েছি…!
মজার ব্যাপার, লক্ষ করুন~বিদ্যাসাগর চিঠিটি যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩। তিনি বেঁচেছিলেন ৭০ বছর ১০ মাস ৩দিন।
অনেক বিখ্যাত মানুষ প্রথম বয়সের বহু ধারণা পরে আর বহন করেননি। দেখা গেছে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবোধ পাল্টে গেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। এক, রবীন্দ্রনাথ মাইকেলকে তুলোধুনা করেছিলেন জীবনের শুরুর দিকে। পরে মাইকেল সম্পর্কে সেই আক্রমণ যে ঠিক ছিল না, তা বলে গেছেন। দুই, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষাকে সরিয়ে ওই দুই প্রদেশে বাংলার প্রচলন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৮৯৮-এ “ভাষা বিচ্ছেদ” প্রবন্ধে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩৯-৭৪২)। রবীন্দ্রনাথ ৩৭ বছর বয়সে কত বড় ভ্রান্ত ধারণা বহন করেছিলেন ভাবুন। কিন্তু পরিণত রবীন্দ্রনাথ সেটা পরে নিজেই সংশোধন করেন এবং অসমিয়া ভাষা যে স্বতন্ত্র একটি আর্য ভাষা সেটা স্বীকারও করেন।
বিদ্যাসাগর তাই ৩৩ বছর বয়সে সাংখ্য ও বেদান্ত নিয়ে যে ধারণা ব্যক্ত করেন~সেটা নিয়ে পরে আর কোনো দাবি তোলেননি। তবে এই বিষয়ে বিভ্রান্তি বা জট এখনও কাটেনি। তিনি কোন্ সাংখ্য ও বেদান্তের কথা বলেছেন~সেটা নিয়ে এযাবৎ আলোচনা হচ্ছে। কেননা, প্রথম জীবনে এরকম বলে থাকলেও পরবর্তী কালে তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন ছিলেন। আর, তাঁর মতামতটি ছিল সরকারি দপ্তরে পাঠানো নথি, কোনো প্রবন্ধ-নিবন্ধ নয়। অজস্র বিষয়ে গোটা জীবন তর্ক করেছেন~কিন্তু এই বিষয়ের সমর্থনে পরে কোনো গম্ভীর আলোচনা করেছেন কি? তাঁর এই নীরবতার কারণ কী? যিনি ৩৩ বছর বয়সে সাংখ্য বা বেদান্ত নিয়ে সরকারি নথিতে টিপ্পনী দিচ্ছেন মাত্র একটি বাক্যে, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের অত বড় পণ্ডিত এর পর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নিদেন একটা প্রবন্ধও কি লিখতে পারতেন না?
এই নিয়ে সবচেয়ে মোক্ষম কথা বলেছেন শংকরীপ্রসাদ বসু। তিনি লিখছেন : ” তেত্রিশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্তদর্শকে ভ্রান্ত দর্শন বলছেন। তাঁর এই কথার উপরে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাঁইত্রিশ বৎসরে তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী থেকে বেদান্তকে বাদ দেবার প্রস্তাবের দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিলেন, তা অনেকেই দেখতে চান না।”(“রসসাগর বিদ্যাসাগর”,দে’জ, দ্বিতীয় সং, ১৯৯২, পৃ. ৩৮)।
ভারতীয় ধর্ম-দর্শনকে নিজের জীবন থেকে কি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছিলেন তিনি? তাহলে তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত “সর্বদর্শন-সংগ্রহ” বইয়ের ভূমিকায় কেন লিখলেন : “সর্বদর্শন-সংগ্রহের মধ্যে সংক্ষেপে সকল ভারতীয় দর্শনের বিবরণ রহিয়াছে, সেইজন্য ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।(তদেব, পৃ.৩৮)। এছাড়া তিনি “আখ্যানমঞ্জরী”-তে যেসব রচনা লিখছেন~সেগুলোর নাম লক্ষ করুন : “ধর্মভীরুতা”, “ধর্মপরায়ণতা”, “ধর্মশীলতার পুরস্কার”, “ন্যায়পরতা ও ধর্মশীলতা”, “ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস”, “যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ”।
সব শেষ রচনাটির শেষে তিনি লিখছেন : “ধর্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্যলাভ ঘটে। ধার্মিক ব্যক্তিকে যদিও কোনও কারণে আপাতত কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয়লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।”
“আখ্যানমঞ্জরী”র বহু রচনায় ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপটি সম্পর্কে লিখেছেন বিদ্যাসাগর।
তাঁর জীবনীতে আছে~প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। পরে “নানা মতভেদ নিবন্ধন ও অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল”। তিনি সরে এলেন।(“বিদ্যাসাগর”, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় সং, পৃ. ৫৩৯)।
আরেকটি প্রসঙ্গ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। “বোধোদয়” গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কোনো ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছিল না। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুযোগে পরের সংস্করণে তিনি “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন”~এইরকম মন্তব্য যুক্ত করেন। তবে ছোটদের পাঠ্যপুস্তকে এহেন গভীর কথা দেওয়ায় স্বামী বিবেকানন্দও নাকি রসিকতা করে উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। তা হাসুনগে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনোভূমির সুপ্ত একটা দিক যে এতে উদ্ভাসিত~তা তো অস্বীকারের উপায় নেই।
তবে, প্রচলিত ধর্ম নিয়ে তিনি বরাবর উদাসীন ছিলেন। আবার নানা ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে তিনি প্রবল প্রতাপী সংস্কারক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে গেছেন~তিনি ধরা দেননি। নিজেকে নোনাজল বলে মৃদু রসিকতা করেছেন। কথামৃত প্রণেতা শ্রীম চেঙ্গিশ খাঁর উদাহরণ দিয়ে বিদ্যাসাগরের “অভিমান” প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে ঈশ্বরে অস্তিত্বে তাঁর সংশয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই ভাষ্যটি বিদ্যাসাগরের নিজের ছিল না। ছিল শ্রীম-র জবানিতে। শোনা কথা। তথাকথিত প্রগতিশীলরা সেটা বিদ্যাসাগরের বলে বাজারে ছাড়ে। একেই বলে “বুর্জোয়ামি”। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়ার ভালো বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন~”পরশ্রমজীবী”!
শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কথা তাঁর মনে কি আলোড়ন তুলেছিল? রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন : “অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও অন্য কাজ কমে যাবে।”
বিদ্যাসাগর কি জীবনের উপান্তে সেই সোনার সন্ধান পেয়েছিলেন!! চরম মানসিক কষ্টের সময় অখিলউদ্দিন নামে এক অন্ধ বাউলকে ডেকে গান শুনতেন। যে-গান ছিল দেহতত্ত্ব মনোশিক্ষার গান~নিজের ভেতরে সত্তারূপী পরমপুরুষের সাধনার গান। ওই গানে আছে~
“কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্ণয় করবে রে কে,
তুমি কোনখানে যাও কোথায় থাকো রে মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ।” বা~
“আপনার নামটি রাখব কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা।”(চণ্ডীচরণের প্রগুক্ত গ্রন্থ, ৫৪৪)।
৩.
সারাটা জীবন পৈতে ফেলেননি তিনি। অথচ তাঁর ওপর কথা বলার মতো কে ছিল? বাবা-মা? কিন্তু পিতামাতার প্রয়াণের পরও পৈতে বহন করেছেন। পিতামাতার শ্রাদ্ধ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলের মতন করেছেন। ঔর্ধ্বদৈহিক অনুষ্ঠান আর কৃচ্ছ্র শৌচকর্মাদি নির্বাহ করেছেন। পারিবারিক জন্মমৃত্যুবিবাহ ইত্যাদিতে স্মার্ত ক্রিয়াকর্ম করতেন। চিঠির উপরে “শ্রীহরি শরণং” লিখতেন। এখন তো দেখি তথাকথিত নাস্তিক-মাওবাদী বাবার মৃত্যুর পর কিছু করেনি~সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করে। এই দেশের তথাকথিত সেকুলার মার্ক্সবাদীদের মতন ঈশ্বর-বিষয়ক কিছু পেলেই উদ্যত মুষল নিয়ে ছুটতেন না।
একটি অসাধারণ তথ্য দিই। এই তথ্য বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীতেই নেই। এটি উদ্ধার করেছেন বিশিষ্ট গবেষক স্বপন বসু। প্রথম জীবনে গায়ত্রী মন্ত্র মনে রাখতে পারতেন না বিদ্যাসাগর, ভুলে যেতেন সন্ধ্যা-আহ্নিকের বা আহার-আচমনের মন্ত্রটন্ত্র। ফলে পিতা “বিলক্ষণ প্রহার”ও করতেন। অথচ শেষ জীবনে সেই বিদ্যাসাগর নিয়মিত নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন। স্বপন বসু এই তথ্য দিয়েছেন মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের “শ্রুতি-স্মৃতি”, প্রথম ভাগ(১৩৩৪, পৃ. ৯৭) থেকে। (“সমকালে বিদ্যাসাগর”, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৫)। স্বপনবাবু জানাচ্ছেন~এমনকি বিভিন্ন হিন্দু ধর্মরক্ষা সমিতির সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলতেন।
৪.
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করি। এটা বিদ্যাসাগর-বিষয়ক কোনো বইয়ে, সংকলনে পাইনি।
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা প্রভাবতী মাত্র তিন বৎসর বয়সে মারা যায়। শিশুকন্যাটিকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একটি ছোট রচনার মধ্যে তিনি তাঁর মনের কষ্ট ধরে রেখেছিলেন। নাম~”প্রভাবতী সম্ভাষণ”। রচনাটির একেবারে শেষে বিদ্যাসাগর লিখছেন : “বৎসে, তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই~যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের, এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।”(বিদ্যাসাগর রচনা-সমগ্র, রিফ্লেক্ট, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃ. ৫৯৬ )।
“যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও”~এই বাক্যটি পড়ে চমকে উঠতে হয়। প্রশ্ন জাগে~বিদ্যাসাগর কি তবে পুনর্জন্মেও বিশ্বাস রাখতেন?
২৭-৯-২০
ডা. প্রশান্ত চক্রবর্তী,
গুয়াহাটি,ভারত।